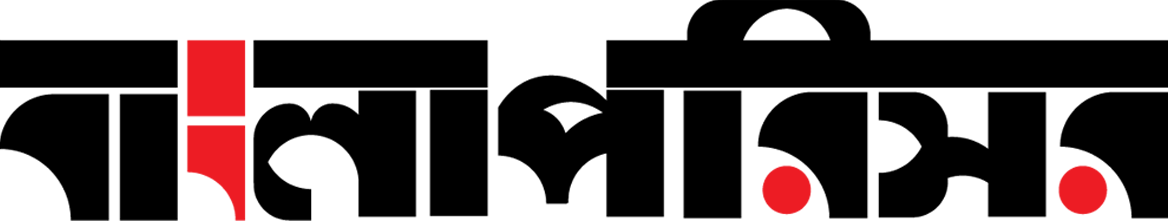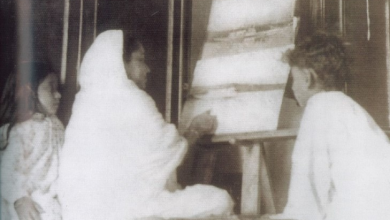জঁ-লুক গদার: নিউ ওয়েভে ভেসে যাওয়া জীবন ও সিনেমার যাত্রা

চিন্ময় ঘোষ:
২০২২ সালের সেপ্টেম্বরের এক সকালে চলচ্চিত্র জগৎ হারায় তার এক অনন্য বৈপ্লবিক স্রষ্টাকে—জঁ-লুক গদার। মৃত্যুর ঠিক আগে তিনি বলেছিলেন, “আর মাত্র দুটি স্ক্রিপ্ট বাকি। তারপরই বিদায়।” বাস্তবতা বলছে, তিনি চিরতরের জন্য বিদায় নিলেন; কিন্তু রেখে গেলেন এমন এক উত্তরাধিকার, যা প্রতিটি সিনেমা প্রেমিক, স্বাধীন নির্মাতা ও চিন্তাশীল দর্শকের মানসপটে জ্বলন্ত নক্ষত্র হয়ে রয়ে যাবে।
জঁ-লুক গদারের জন্ম ১৯৩০ সালের ৩ ডিসেম্বর, প্যারিসে। উচ্চবিত্ত পরিবারে জন্ম হলেও তার চিন্তার গ্রাফ বরাবরই সমাজের মূলধারার বিপরীতে ছিল। শুরুতে গণিত নিয়ে পড়ালেখা করলেও খুব শীঘ্রই তিনি বুঝতে পারেন যে তার ভবিষ্যৎ এ প্যাটার্নে গাঁথা নেই। গণিতে ব্যর্থ হয়ে নৃবিজ্ঞান পড়তে শুরু করেন, আর এরই মধ্যে সিনেমার প্রতি গভীর মোহ তাকে গ্রাস করে নেয়।
মাত্র ১৯ বছর বয়সেই তিনি ফিল্ম ক্রিটিক হিসেবে লেখালেখি শুরু করেন। তিনি যুক্ত হন কাইয়ে দ্যু সিনেমা ম্যাগাজিনে, যেখানে তার সহকর্মী ছিলেন ফ্রঁসোয়া ত্রুফো, এরিক রোমের, ক্লদ শেব্রলদের মতো পরবর্তীতে কিংবদন্তি হয়ে ওঠা নির্মাতারা। এখান থেকেই গদার নিজস্ব ভাষা, দর্শন এবং দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেন—যার পেছনে ছিল ‘অ্যুত্যর থিওরি’, অর্থাৎ পরিচালকই সিনেমার লেখক।
নিউ ওয়েভ এবং ‘ব্রেথলেস’-এর বিপ্লব
১৯৬০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ব্রেথলেস’ (À bout de souffle) সিনেমা দিয়ে গদার সিনেমার বিশ্বমঞ্চে প্রবল ঝড় তোলেন। এই চলচ্চিত্রে আমরা দেখি এক তরুণ চোর ও তার প্রেমিকার সম্পর্কের দ্বন্দ্ব, যা ক্রমেই বিশ্বস্ততা, বিশ্বাসঘাতকতা ও অস্তিত্ববাদী প্রশ্নের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু এই গল্পের চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল তার নির্মাণ কৌশল।
এই সিনেমায় গদার ব্যবহার করেন জাম্প কাট, হ্যান্ডহেল্ড ক্যামেরা, ন্যাচারাল লাইটিং, অগোছালো সংলাপ ও রূঢ় বাস্তবতা। দর্শক যেন বিভ্রান্ত হন, সেই উদ্দেশ্যেই যেন ভুল এডিটিং করেন। কারণ, গদারের মতে, জীবন নিজেই এক জটিল, অসংলগ্ন অভিজ্ঞতা, যা সিনেমার নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রকাশ পায় না। তিনি বলেছিলেন, “জীবন অনেক সময় গল্পের চাইতেও বেশি জটিল।”
ফরাসি নিউ ওয়েভ (Nouvelle Vague) শুধু একটি সিনেমার আন্দোলন নয়; এটি ছিল সমাজ, সংস্কৃতি এবং দর্শনের এক উত্তাল প্রতিক্রিয়া। গদার ছিলেন এর সর্বাগ্রে, একজন অগ্রদূত, যিনি সিনেমার ব্যাকরণকেই অস্বীকার করে এক নতুন ভাষার জন্ম দেন। রজার ইবার্ট তাই ‘ব্রেথলেস’-এর রিভিউতে লেখেন, “Modern Movies Begin Here”—এই সিনেমা দিয়েই আধুনিক সিনেমার যাত্রা শুরু।
প্রতিদিনের গল্পে রাজনৈতিক চেতনা
গদারের প্রতিটি সিনেমা যেন একেকটি সমাজতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপকথা। ‘ভিভ্রে স্যা ভি’তে (Vivre sa vie, ১৯৬২) তিনি যৌনকর্মী নারীর মাধ্যমে তুলে ধরেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অমানবিকতা। ‘উইকএন্ড’ (Weekend, ১৯৬৭) সিনেমায় মধ্যবিত্ত জীবনের উপর খরস্রোতা ব্যঙ্গ, আর ‘সিম্প্যাথি ফর দ্য ডেভিল’ (১৯৬৮)–এ তুলে আনেন রাজনৈতিক ডিসকোর্স ও বিপ্লবী ভাবনা।
গদারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে প্রকাশ পায় ১৯৬৮ সালের ফরাসি ছাত্র আন্দোলনের সময়। সে বছরের কান চলচ্চিত্র উৎসব বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে তিনি অবস্থান নেন, বলেছিলেন, “আমরা কি এখানে ফিল্ম দেখাতে এসেছি, যখন রাস্তায় ছাত্ররা মার খাচ্ছে?” গদারের কাছে সিনেমা কেবল বিনোদন নয়; বরং তা ছিল প্রতিবাদ, প্রশ্ন তোলা এবং সমাজ বদলের এক হাতিয়ার।
জীবন ও সিনেমার মধ্যবর্তী সীমানা
জঁ-লুক গদারের জীবনের গল্প নিজেই যেন এক সিনেমার কাহিনি। সিনেমার জন্য পরিবার ত্যাগ, চুরি করা, জেল খাটা—সবই করেছেন সিনেমা নির্মাণের জন্য। এমনকি সিনেমার মধ্যে তিনি নিজের জীবনের গল্পও মিশিয়ে দিয়েছেন, যেমন ‘ব্যান্ড অব আউটসাইডারস’-এ স্ত্রী আনা কারিনাকে মায়ের অনুরূপ চরিত্রে অভিনয় করিয়েছেন।
গদার কখনোই নিজেকে কেবল একজন পরিচালক হিসেবে ভাবেননি। তিনি ছিলেন একজন লেখক, চিন্তক এবং সর্বোপরি একজন ‘সিনেম্যাটিক ফিলোসোফার’। তার বইগুলো—‘গদার অন গদার’, ‘হিস্টোয়ার দ্যু সিনেমা’, ‘ফিউচার অব ফিল্ম’, ‘লেটার টু জেন’—সবই আমাদের দেখায় গদারের অভ্যন্তরীণ জগৎকে, তার দর্শন, দ্বিধা এবং বিস্ময়কে।
সমালোচনা, আত্মসমালোচনা ও দর্শক বিমুখতা
গদারের সিনেমা নিয়ে বিতর্ক কখনো থেমে থাকেনি। ইংমার বার্গম্যান বলেছিলেন, “গদার সিনেমা বানান কেবল সমালোচকদের খুশি করার জন্য।” অনেকেই মনে করেন, তিনি দর্শকের চাহিদাকে উপেক্ষা করে বরাবরই একটি ‘অভিজাত’ দৃষ্টিকোণ থেকে সিনেমা নির্মাণ করতেন। গদার নিজেও এক পর্যায়ে বলেন, তিনি ‘সেল্ফ-অবসেশনের’ শিকার হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এই আত্মসচেতনতা, এই আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়েই তিনি আবার নতুন এক দিগন্তের দিকে এগিয়ে যান।
শেষযাত্রার এক্সপেরিমেন্ট
জীবনের শেষ সিদ্ধান্তটিও তিনি নিয়েছেন নিজের মতো করে। গদার বেছে নেন অ্যাসিস্টেড সুইসাইড, কারণ তার মতে, শরীর ও মন আর সিনেমার জন্য উপযোগী ছিল না। এও যেন এক শেষ প্রতীকী বিবৃতি—নিজের জীবন, নিজের মতো করেই শেষ করলেন তিনি।
উত্তরাধিকার ও প্রভাব
গদার আমাদের শিখিয়েছেন, সিনেমা কেবল গল্প বলার একটি মাধ্যম নয়, এটি দর্শন, রাজনীতি, এবং নান্দনিকতার এক অভূতপূর্ব সম্মিলন। তার কারণে আজ আমরা সিনেমায় মার্কসবাদের কথা বলতে পারি, জায়নিজমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি, প্রান্তিকের জীবনের গল্প তুলে ধরতে পারি। গদার ছিলেন সেই নির্মাতা, যিনি স্বাধীনতা ও প্রশ্ন তোলাকে একধরনের নৈতিক দায়িত্বে রূপ দিয়েছিলেন।
তিনি একবার বলেছিলেন, “জীবন কেবল সিনেমার একটি অংশ নয়; সিনেমা হলো অনেক জীবনের টুকরোর সমষ্টি।”
আজ তার অনুপস্থিতিতে আমরা যদি সেই স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারি, নতুন চিন্তা, নতুন নির্মাণ ও নতুন প্রশ্নের জন্ম দিতে পারি, তবেই গদারের নিউ ওয়েভের ঢেউ থামবে না।