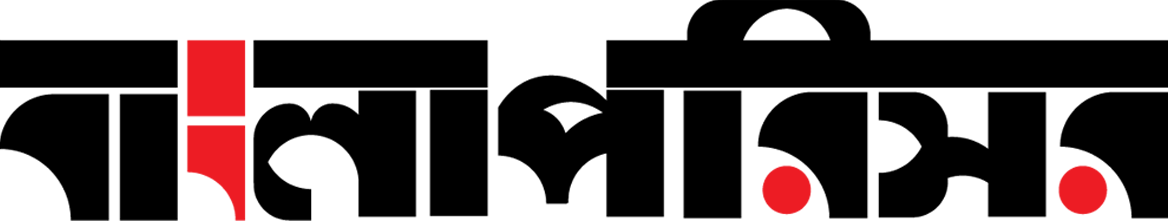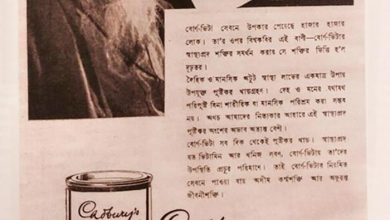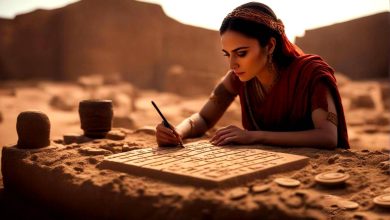বঙ্গভঙ্গ: শেকড়ের ইতিহাস

রিমন দে
ব্রিটিশ ভারত ও বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তখনকার বাংলা প্রদেশ ছিল বিশাল—এর মধ্যে ছিল আজকের বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসামের কিছু অংশ এবং মধ্যপ্রদেশের কিছু এলাকা। এ বিশাল অঞ্চলের প্রশাসন চালানো হয়ে উঠেছিল কষ্টসাধ্য। তাই ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জন বাংলা প্রদেশকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বাংলা বিভক্ত হয়। পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে গঠিত হয় একটি নতুন প্রদেশ, যার রাজধানী হয় ঢাকা। আর পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় অপর প্রদেশ, যার রাজধানী ছিল কলকাতা। ইতিহাসে এই ঘটনাটিই বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত।
বঙ্গভঙ্গের পেছনে প্রশাসনিক কিছু যুক্তি থাকলেও, এর রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল অনেক বড়। এই বিভক্তির ফলে বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভাজনের রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মীয় বিভাজন তৈরি করে জাতিয়তাবাদী আন্দোলন দুর্বল করতে চেয়েছিল।
তবে এর পেছনে প্রশাসনিক অজুহাতও ছিল। বাংলা প্রদেশ এত বড় ছিল যে, একজন গভর্নরের পক্ষে এর কার্যকর শাসন কঠিন হয়ে উঠেছিল। উড়িষ্যার ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সরকারের ব্যর্থতা পর্যালোচনা করতে গঠিত কমিটি একে প্রশাসনিক সমস্যার ফল বলেই মনে করেছিল। এরপর একের পর এক শাসনকর্তা ও ব্রিটিশ কর্মকর্তা বাংলা বিভক্তির প্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন। ১৮৭৪ সালে আসামকে আলাদা করে চিফ কমিশনারের অধীনে আনা হয়। লর্ড কার্জন এসব আগের প্রস্তাব ও বাস্তবতাগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা এগিয়ে নেন।
কার্জনের যুক্তি ছিল—কলকাতাকেন্দ্রিক প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিম বাংলাকেই সব সুযোগ দিয়েছে, আর পূর্ব বাংলা অবহেলিত থেকে গেছে। তাই পূর্ব বাংলার উন্নয়নের জন্য আলাদা প্রদেশ প্রয়োজন। তিনি নিজেই পূর্ববাংলা সফর করে এ অঞ্চলের সম্ভাবনা দেখতে পান এবং ঢাকাকে রাজধানী করে নতুন প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গঠন, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থান তৈরির চিন্তা ছিল।
অর্থনৈতিক বৈষম্যও ছিল বঙ্গভঙ্গের আরেকটি বড় কারণ। পূর্ববাংলার জমির মালিকদের অধিকাংশই কলকাতায় বসবাস করতেন। তারা স্থানীয় কৃষকদের নিপীড়ন করে রাজস্ব আদায় করতেন, কিন্তু সে অর্থের কোনো অংশই এলাকাবাসীর উন্নয়নে খরচ হতো না। যোগাযোগ ব্যবস্থা, পুলিশি নিরাপত্তা, ডাক ব্যবস্থা—সব ছিল দুর্বল। ব্রিটিশ সরকার চেয়েছিল এই সমস্যাগুলোর সমাধান করে একটি কার্যকর প্রশাসন গড়ে তুলতে।
তবে বঙ্গভঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি ছিল রাজনৈতিক। ইংরেজরা জানত, কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণিই ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এদের দুর্বল করতে পারলেই ভারতের রাজনৈতিক জাগরণকে থামিয়ে দেওয়া যাবে। তাই হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিম বাংলা ও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলা আলাদা করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা হয়। এতে মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশপ্রীতি তৈরি হয়, আর হিন্দুদের মধ্যে ক্ষোভ জন্ম নেয়। কলকাতায় বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়, গড়ে ওঠে স্বদেশি আন্দোলন। হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণি ও সংবাদপত্র এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়।
ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে—কারও মতে বঙ্গভঙ্গের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক সমস্যা সমাধান, আবার কারও মতে এটি ছিল নিখাদ রাজনৈতিক চাল। ব্রিটিশপন্থী ঐতিহাসিকেরা যেমন রিজলে, ইবেৎসেন প্রমুখ প্রশাসনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আর জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মতে এটি ছিল হিন্দু-মুসলমানকে আলাদা করে শাসন টিকিয়ে রাখার কৌশল।
বঙ্গভঙ্গ তাই শুধু একটি প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস নয়, এটি হয়ে ওঠে বাংলার জাতীয় চেতনার গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল। পরবর্তী সময়ে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহার করা হলেও বাংলার ইতিহাসে এর ছাপ চিরস্থায়ী হয়ে থাকে।
বাংলাপরিসর/ডিএম