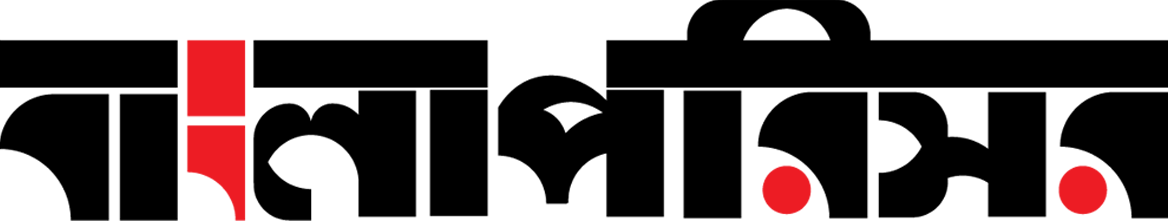বাংলার প্রথম নারী চিত্রশিল্পী নবাবজাদী মেহেরবানু খানমের শিল্পভুবন

সৌরভ শিমুল
বাংলা মুসলিম নারীর আত্মপ্রকাশের ইতিহাসে নবাবজাদী মেহেরবানু খানম একটি উজ্জ্বল ও ব্যতিক্রমী নাম। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ঢাকার সমাজে যখন পুরুষরাই ছিলেন সাংস্কৃতিক অগ্রগতির মূল চালক, সেই সময়েই এক নারী ঘরের আড়াল থেকে রঙ-তুলি হাতে গড়ে তুলেছিলেন তার নিজস্ব শিল্পজগত। তিনি শুধু ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য ছিলেন না, বরং ছিলেন সৃজনশীলতা, সংবেদনশীলতা এবং প্রগতির এক অনন্য প্রতীক। শিল্প, শিক্ষা, সমাজসেবা এবং সাহিত্য অনুরাগের অপূর্ব সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল তার জীবনের রূপরেখা।
নবাবজাদী মেহেরবানু খানমের জন্ম হয় ঢাকার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ও প্রভাবশালী পরিবারে। তার পিতা ছিলেন স্যার নবাব খাজা আহসানুল্লাহ, যিনি শুধু জমিদার নন, বরং ব্রিটিশ ভারতের এক সুপরিচিত সমাজসংস্কারক এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব। মেহেরবানুর মা কামরুননেসা খানম, যাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তার কন্যারা ‘কামরুননেসা বালিকা বিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠা করেন, ছিলেন পারিবারিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক। পরিবারে ছিল চারপাশ জুড়ে জ্ঞানের পরিমণ্ডল—বইপত্র, সাহিত্যিক আলোচনা, রাজনৈতিক বিতর্ক, এবং শিল্পানুরাগে গড়ে উঠেছিল এক ঘরোয়া শিক্ষাভিত্তিক আবহ।
তার পিতামহ নবাব আবদুল গণি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ‘নবাব’ উপাধি প্রাপ্ত হন এবং তার সময়ে আহসান মঞ্জিল নির্মিত হয়। এই পরিবারে পুরুষরা যেখানে রাজনীতি, সমাজসংস্কার ও জমিদারিত্বে ব্যস্ত ছিলেন, নারীরা সেখানে ঘরোয়া পরিবেশেই গড়ে তুলেছিলেন এক মননশীল জগত। এই জগতে বড় হয়ে উঠেন মেহেরবানু।
মেহেরবানুর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক ছিল তার বিয়ে। ১৯০১-০২ সালের দিকে তার বিয়ে হয় খান বাহাদুর খাজা মোহাম্মদ আজমের সঙ্গে—একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সম্পাদক, রাজনীতিক ও সমাজকর্মী। তিনি ছিলেন ঢাকা কলেজের ছাত্র এবং সাহিত্য ও সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ব্যক্তিত্ব। তার অনুবাদে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বড় বউ’ উপন্যাসটি উর্দু ভাষায় ‘বড়ী বহু’ নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে।
খাজা আজম মেহেরবানুর শিল্পপ্রতিভার প্রশ্রয়দাতা ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, একজন নারীও ঘরের দায়িত্ব পালন করেও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারেন। সেই কারণে তিনি শুধু মেহেরবানুর শিল্পচর্চায় উৎসাহ দেননি, বরং তাদের দিলকুশার বাসভবনকে গড়ে তোলেন এক শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র হিসেবে। সেই বাড়িতে ছিল দেশ-বিদেশের বিখ্যাত চিত্রকর্ম, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা এবং আলোচনার আসর।
মেহেরবানু খানম কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তার চিত্রশিল্পের শিক্ষাও ছিল একান্তই স্বশিক্ষিত। তিনি কেবল ছয় মাস একজন ব্যক্তিগত শিক্ষকের কাছ থেকে চিত্রাঙ্কনের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। এই স্বল্প সময়ের প্রশিক্ষণেই তিনি যে দুইটি চিত্র এঁকেছিলেন, তা প্রকাশিত হয় উর্দু ভাষার প্রভাবশালী পত্রিকা মোসলেম ভারত-এ। চিত্র দুটি ছিল—একটি খেয়া পারাপারের দৃশ্য এবং অন্যটি বিক্রমপুরের তালতলার পল্লীদৃশ্য। এই চিত্রগুলোর সংবেদনশীল রূপায়ণ, প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পীর আত্মিক সংযোগ এবং নিখুঁত আলোক-ছায়ার ব্যবহার দেখে তৎকালীন সাহিত্যিক, কবি ও সমালোচকেরা বিস্মিত হন।
তার আঁকা নৌকার দৃশ্য দেখে কাজী নজরুল ইসলাম রচনা করেন ‘খেয়াপারের তরণী’ কবিতাটি। এই ঘটনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে চিত্রশিল্প ও কবিতার এক অপূর্ব সংযোগ ঘটে, যার মূলে ছিলেন এই নিভৃতচারিণী নারী।
মেহেরবানুর সন্তানরাও ছিলেন সৃজনশীল চর্চার ধারক ও বাহক। তার পুত্র খাজা মোহাম্মদ আদিল ছিলেন উর্দু কবি ও সাহিত্যিক। তিনি হেকিম হাবিবুর রহমানের সম্পাদিত পত্রিকা যাদু-এর পুনঃপ্রকাশ ঘটান। অপর পুত্র খাজা মোহাম্মদ আজমল ছিলেন ঢাকার প্রথম চলচ্চিত্র ‘দ্য লাস্ট কিস’-এর পরিচালক, চিত্রগ্রাহক, অভিনেতা ও সম্পাদক। মেয়ের বিয়ে হয় খাজা মোহাম্মদ আজাদের সঙ্গে, যিনি একই চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রাহক ছিলেন।
তাদের পরিবার হয়ে উঠেছিল ঢাকার প্রথমদিককার চলচ্চিত্র, সাহিত্য ও রেডিও জগতের অনুরাগীদের কেন্দ্রবিন্দু। মেহেরবানুর উত্তরাধিকার কেবল তার আঁকা ছবি নয়, বরং তার সন্তানদের মধ্য দিয়েও বিস্তৃত হয়েছে বহু সাংস্কৃতিক পরিসরে।
মেহেরবানু শুধু চিত্রশিল্পী নন, ছিলেন সমাজসেবিকাও। তিনি বাংলাবাজারে নারীদের জন্য একটি স্কুল স্থাপনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। অনাথ শিশুদের আশ্রয় দেওয়া এবং লালন-পালনের দায়িত্ব নেয়াও ছিল তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সমাজের অবহেলিত মানুষদের প্রতি তার সহানুভূতি ছিল অকৃত্রিম।
তিনি ছিলেন দানশীলা, স্নেহময়ী এবং জ্ঞানচর্চায় আগ্রহী এক মহীয়সী নারী, যাঁর জীবন কেবল নবাব পরিবারে সীমাবদ্ধ থাকেনি—তার কর্মে, চেতনায়, নীরব প্রচেষ্টায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন একটি সময়ের সাক্ষ্য।
১৯২৫ সালের ৩ অক্টোবর নবাবজাদী মেহেরবানু খানম মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে ঢাকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি মহলে নেমে আসে শোকের ছায়া। খাজা শামসুল হকের রোজনামচায় পাওয়া বর্ণনা অনুযায়ী, তার মৃত্যুতে নবাব পরিবারের সকল সদস্য শোকাহত হন। দিলকুশা মসজিদের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়।
মেহেরবানু খানম ছিলেন সময়ের ঊর্ধ্বে এক প্রগতিশীল মননের প্রতিচ্ছবি। তার চিত্রশিল্প, সাহিত্য অনুরাগ, পারিবারিক জীবন, সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক উৎসাহ সবকিছু মিলিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ। তার জীবন কাহিনি প্রমাণ করে, নারীশক্তি নিছক পরিবার বা সমাজ দ্বারা নির্ধারিত নয়—যে নারী নিজস্ব সত্তাকে আবিষ্কার করেন, তিনিই ইতিহাসে নিজের জন্য স্থান করে নেন।
বাংলাপরিসর/ডিআর